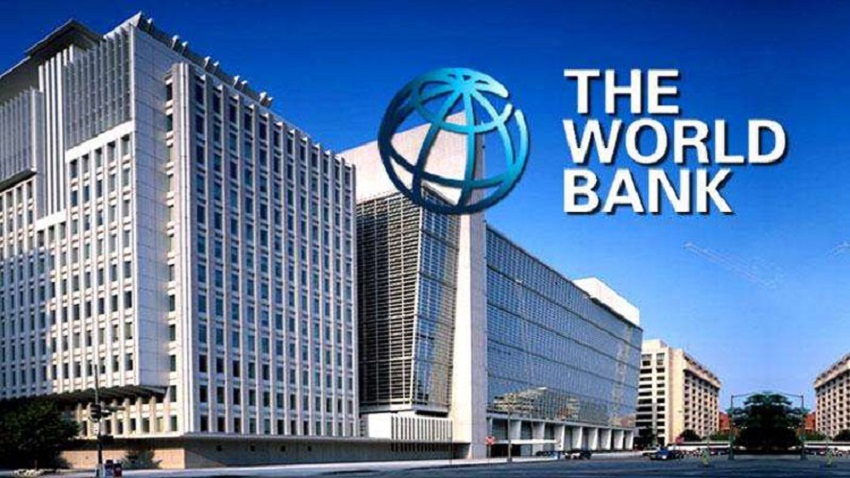গুমবিষয়ক কমিশনের প্রতিবেদন : জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি ও নির্যাতন বিচারব্যবস্থাকে করেছে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার-নিযুক্ত গুমবিষয়ক কমিশনের দ্বিতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের আশ্রয় নেওয়া হতো। এ ধরনের নির্যাতন শুধু ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত করেনি, বরং দেশের বিচারব্যবস্থার ওপরও গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত সরকারের সময়ে গুম ও নির্যাতন একপ্রকার ‘প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি’ হিসেবে গড়ে উঠেছিল, যা ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে নিরাপদ বলয়—নিজ বাড়ির মধ্যেও—মানুষকে ভীত ও শঙ্কিত করে তোলে। এই ভয়-ভীতির আবহে অনেক পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক অবসাদে ভুগেছে।
কমিশন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ওই সময় জোরপূর্বক আদায়কৃত স্বীকারোক্তিগুলোর ধরন প্রায় একই রকম এবং পূর্বনির্ধারিত ভাষায় রচিত হতো, যা বিচারপ্রক্রিয়াকে বিকৃত করে তোলে। এসব স্বীকারোক্তি অপরাধের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের পরিবর্তে কেবল দোষী সাব্যস্ত করাকে অগ্রাধিকার দিত। এতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ হ্রাস পায় এবং অপরাধী শনাক্তের বদলে নিরীহ নাগরিকদের হয়রানি করা হতো। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তদন্তের প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রতার ঘাটতির কারণে এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রায়শই ব্যবহার করা হতো প্রমাণ সংগ্রহ, সাক্ষ্য যাচাই কিংবা দায়িত্বে অবহেলার দায় এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে। এতে করে বিচারিক ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। এমনকি যখন বেআইনি আটক, নির্যাতন, আইনজীবীর অনুপস্থিতি বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটির প্রমাণ থাকত, তখনও সেই স্বীকারোক্তিই বিচারিক রায়ে প্রাধান্য পেত। কমিশন আরও জানিয়েছে, যেসব মামলায় হেফাজতে স্বীকারোক্তি ছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে আদালত থেকে জামিন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে, যেসব মামলায় স্বীকারোক্তি ছিল না, সেগুলোর ক্ষেত্রে জামিনের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকত।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই পরিস্থিতি শুধু বিচারের নিরপেক্ষতা ব্যাহত করেনি, বরং একটি সক্রিয় নাগরিক সমাজকে দমন করতেই বিচারব্যবস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে তৎকালীন সরকার। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিরোধী মত দমন করতে বিচারব্যবস্থা, পুলিশ ও প্রশাসনের অপব্যবহার করেছে। সাহসী সাংবাদিক, শ্রমিক নেতা, বিরোধী দলের আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী, লেখক ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ভয়ভীতি, হয়রানি, অবৈধ গ্রেপ্তার, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার মতো ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ মামলাই নির্বাচনপূর্ব সময়ে করা হতো, যার মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠকে দমন করা সহজতর হতো। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তদন্ত সংস্থা, রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি এবং বিচারক এই তিন স্তরের কার্যকর ভূমিকা ছাড়া ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। তদন্ত যদি সুষ্ঠুভাবে না হয়, তবে বিচার প্রক্রিয়া সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে না। কারণ, একটি ফৌজদারি মামলার ভিত্তি হলো সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত চার্জশিট, আর তা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাহলে ন্যায়বিচার অর্জনের কোনো সুযোগই থাকে না। কমিশন মনে করে, তদন্ত কর্মকর্তা যদি আন্তরিকতা, দক্ষতা ও পেশাগত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া পড়ে বিচারব্যবস্থার সর্বত্র। বিচারক যেন একজন আম্পায়ারের মতো নিরপেক্ষ থেকে মামলার উভয় পক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেন—এটাই প্রত্যাশিত বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে শেষ পর্যন্ত বলা হয়, তদন্ত সংস্থা, কৌঁসুলি ও বিচারকদের জবাবদিহির আওতায় আনতে কার্যকর পর্যবেক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। কেউ দায়িত্বে অবহেলা করলে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপযুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।